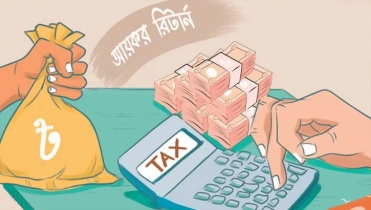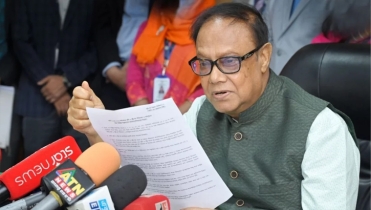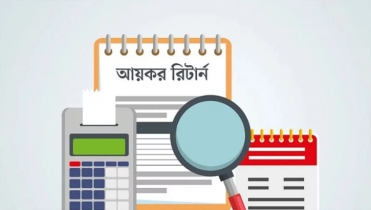আমদানি নিষিদ্ধ ভেপের জমজমাট বাজার
ধূমপানের ক্ষতি হ্রাসে কার্যকর বিকল্প হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হলেও বাংলাদেশে আমদানি নিষিদ্ধ ই-সিগারেট বা ভেপ । তবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে অবৈধভাবে আমদানিকৃত ভেপ পণ্য।
অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ঢাকার অন্তত ৮ থেকে ১০টি এলাকায় গড়ে উঠেছে ভেপবিক্রির 'হটস্পট' । ফুটপাত থেকে শুরু করে জুতা ও কসমেটিকসের দোকানের আড়ালে চলছে এই ব্যবসা । শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন শপের মাধ্যমেও সরবরাহ করা হচ্ছে এসব পণ্য। এ বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই । ফলে মান নিয়ন্ত্রণহীন ভেপ পণ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার।
চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় । ঐ প্রজ্ঞাপনে ‘আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪'-এর আওতায় আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় ই-সিগারেট যুক্ত করা হয়েছে । যদিও দেশে ই-সিগারেট বা ভেপ পণ্যের বিষয়ে এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি।
ভেপ কী?: ধূমপানের ক্ষতি কমানোর বিকল্প পণ্য হিসেবে ভেপ বা ই-সিগারেট ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এটি একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিভাইস, যা তামাক পোড়ানো ছাড়াই ব্যবহারকারীকে নিকোটিন গ্রহণের সুযোগ দেয় । সাধারণত ভ্যাপারাইজারে থাকা ই-লিকুইড উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, যেটি ব্যবহারকারী শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করেন ।
ধূমপানের ক্ষতি হ্রাস পণ্য হিসেবে ভেপিং ছাড়াও রয়েছে হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টস, নিকোটিন পাউচ ও স্নাসের মতো বিকল্প। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সুইডেন, ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডে এই পণ্যগুলোকে ধূমপান ছাড়ার কার্যকর সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেখানে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলোর ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশনও (এফডিএ) ভেপ পণ্যের মানদণ্ড বিবেচনা করে এসব পণ্যের বিক্রির অনুমতি দিয়েছে।
উদাহরণ স্বরূপ, সুইডেনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলে দেখা যায়, গত তিন দশকে দেশটির বহু নাগরিক ধূমপান ছেড়ে ‘স্নাস' নামক ধোঁয়াবিহীন ওরাল তামাকজাত পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। সিগারেটের তুলনায় এটি কম ক্ষতিকর এবং তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশটি এই ধরনের পণ্যের ওপর করের হারও কম রেখেছে।
এর ফলে সুইডেন বর্তমানে ইউরোপের মধ্যে ধূমপানজনিত মৃত্যু ও রোগে আক্রান্ত মানুষের হার সবচেয়ে কম—এমন একটি দেশ হিসেবে পরিচিত।অবৈধ ব্যবসায় রাজস্ব ফাঁকি: দেশে কী পরিমাণ ভেপপণ্য বিক্রি হয়, তার সুনির্দিষ্ট কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। তবে সংশ্লিষ্টদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, সারা দেশে ভেপপণ্য বিক্রির পাঁচ শতাধিক খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা রয়েছে। এর বাইরেও সুনির্দিষ্ট
কোনো নীতিমালা না থাকায় গড়ে উঠেছে ভেপপণ্যের অসংখ্য দোকান । প্রতি মাসে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রতিটি দোকানে গড়ে বিক্রির পরিমাণ প্রায় দেড় লাখ টাকার । প্রতি মাসে সারা দেশে গড়ে বিক্রি হয় ৭.৫ কোটি টাকার। আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ার আগে ভেপপণ্যে মোট শুল্ককর ছিল ২৮৯ শতাংশ পর্যন্ত। এ হিসাবে মাসে রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ থেকে ২২ কোটি টাকা, আর বছরে প্রায় ২৪০ থেকে ২৬০ কোটি টাকা । অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ফুটপাত থেকে শুরু করে জুতা ও কসমেটিকস দোকানের আড়ালেও চলছে ভেপ বিক্রি । এমনকি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন শপের মাধ্যমেও সরবরাহ করা হচ্ছে এসব পণ্য ।
রাজধানীতে অবৈধ ভেপ বিক্রির যে ৮-১০টি 'হটস্পট' গড়ে উঠেছে, সেগুলোর মধ্যে নিউ মার্কেট, চকবাজার ও মিরপুর এলাকায় বিক্রি হয় নিম্নমান ও কম দামের চীনা ও মালয়েশিয়ান ভেপ ও ফ্লেভার বিক্রি হয়ে থাকে । ঐ এলাকাগুলোতে ফুটপাতের দোকানি, মোবাইল গেজেট শপ, ঘড়ি ও সানগ্লাস বিক্রেতারা এই পণ্য বিক্রি করছেন ।পান্থপথ, বসুন্ধরা, বনশ্রী ও বাড্ডা এলাকার ভেপ বাজারে তুলনামূলকভাবে দামি ও বিদেশি পণ্য বেশি বিক্রি হয় ।
এখানে ইউরোপ ও যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা উচ্চমূল্যের ভেপ ডিভাইস ও লিকুইড পাওয়া যায়, যা বিক্রি করা হয় ‘এক্সক্লুসিভ পণ্য হিসেবে। এসব বিক্রয় কেন্দ্রমূলত জুতা, বিদেশি জার্সি, হুকা লাউঞ্জ বা বুটিক শপের আড়ালে পরিচালিত হয় । এছাড়াও তাদের অনলাইন-ভিত্তিক ডেলিভারি ও হোম-ডেলিভারি সেবা চালু রয়েছে।
বিক্রেতারা জানান, ভেপের দাম সাধারণত ৩ হাজার থেকে শুরু করে ১২-১৩ হাজার টাকা। আর সঙ্গে আছে ই-লিকুইড, যার দাম ৫০০ থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা । চীনা ও ক্লোন ভেপগুলোর দাম ১ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকার মধ্যে। আর ই-লিকুইডগুলোর দাম ১৫০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত।
বনশ্রীর এক ভেপ ব্যবসায়ী বলেন, প্রতি মাসে ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করি। বিক্রির প্রায় ৩০ শতাংশ আমাদের লাভ। নিউ মার্কেট বা চকবাজারের স্থানীয় পণ্য বিক্রি করলে লাভের পরিমাণ আরো বেশি হয়।নিউ মার্কেটের ভেপ ব্যবসায়ী রাকিব জানান, তার মাসিক বিক্রি ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকার মতো। এর ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত লাভ হিসেবে থাকে । স্থানীয় পণ্যের চাহিদা বেশি থাকায় লাভও বেশি হয়।
নিউ মার্কেট এলাকার একটি পাইকারি ভেপ দোকানের মালিক ইব্রাহিম বলেন, 'আমরা প্রতি মাসে গড়ে ২ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকার ভেপ পণ্য বিক্রি করি। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ হচ্ছে পড সিস্টেম ও ডিসপোজেবল ডিভাইস, আর বাকি ৬০ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের লিকুইড ও এক্সেসরিজ । শুধু ঢাকাতেই নয়, এখন চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য জেলা শহরেও ভেপের বাজার ছড়িয়ে পড়েছে।'বিদেশ থেকে আসা ও দেশের ভেতরে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ভেপ পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের কোনো বালাই নেই । বেশির ভাগই নিম্নমানের হওয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকি না কমে আরো বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
কোথা থেকে কীভাবে আসে: সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কালোবাজারিরা দুটি প্রধান উপায়ে দেশে ভেপ পণ্য আনছে । প্রথমত, ‘লাগেজ পার্টি' বা 'হ্যান্ডক্যারি'র মাধ্যমে বিদেশ থেকে ব্যক্তিগত মালামালের আড়ালে অনেকে ভেপ ডিভাইস ও লিকুইড নিয়ে আসছেন । যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তুলনামূলক মানসম্মত ও উচ্চমূল্যের ভেপ পণ্য চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর ব্যবহার করে দেশে প্রবেশ
করছে।
দ্বিতীয়ত, স্থলবন্দর দিয়ে। ভারতের অবৈধ ভেপ আমদানির সিংহভাগ গুয়াহাটি বিমানবন্দর দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে, সেখান থেকে সেগুলো পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অবৈধ বাজারের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন অঘোষিত সীমান্তপথে এই পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। পাশাপাশি, কিছু ভেপ পণ্য বিভিন্ন সাধারণ পণ্যে ও আড়ালে যেমন ঘড়ি, জুতা, জার্সি বা কসমেটিকস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে শিপমেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা হচ্ছে, যা বর্তমানে মূলত মালয়েশিয়া হয়ে আসে, যদিও খুব অল্প পরিমাণে । অভিযোগ রয়েছে, কিছু কর্মকর্তার সহায়তায় এসব পণ্য কাস্টমস পেরিয়ে বন্দর দিয়ে প্রবেশ করছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাড্ডার একটি ভেপ শপের বিক্রেতা বলেন, 'নিজেরা বা আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে পণ্য আনি। সিলেট বিমানবন্দর ব্যবহার করি এবং সেখান থেকে সড়কপথে ঢাকায় নিয়ে আসি। লোকাল কিছু পণ্য চকবাজার থেকে সংগ্রহ করি।' তিনি আরো বলেন, বর্তমানে যেহেতু আমদানি নিষিদ্ধ, তাই আগে যারা অবৈধভাবে শিশুখাদ্য, কসমেটিকস, ওষুধ ও বিদেশি সিগারেট সরবরাহ করতেন, তারা এখন ভেপ পণ্যে ঝুঁকেছেন, কারণ এতে লাভের পরিমাণ বেশি।
নিউ মার্কেটের ‘এমএক্স১২' শপের এক বিক্রেতা জানান, ‘আমরা কয়েক জন মিলে শিপমেন্টে ভেপ আনি এবং পরে নিউ মার্কেট থেকে শহরের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করি।'খুচরা বিক্রেতা মোশরেফ হোসেন বলেন, 'আমরা পাইকারি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ভেপ কিনি। কিছু পণ্য চকবাজার থেকেও সংগ্রহ করি, তবে সেখানে মূলত জুস, কয়েল আর কাটিজ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেট ও চকবাজারের কিছু বিক্রেতা নিজেরাই কেমিক্যাল ও ফ্লেভার মিশিয়ে জুস তৈরি করে, যা সম্ভবত ক্ষতিকর তবে দাম কম হওয়ায় আমাদের লাভ বেশি।'
ক্রেতা কারা: বাংলাদেশে ভেপ পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ হলেও এর একটি ভোক্তা শ্রেণি গড়ে উঠেছে। ভেপ পণ্যের ব্যবসায়ী ইব্রাহিম বলেন, 'মূলত ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সিদের মধ্যে এসব পণ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নিম্নমানের ও কমদামি ভেপ সহজলভ্য হওয়ায় ১৮ বছরের কম বয়সিদের হাতেও এটি চলে যাচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকার সুযোগ নিয়ে বিক্রি হচ্ছে যত্রতত্র।বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাহাদ আহমেদ বলেন, 'আমি আগে নিয়মিত ধূমপান করতাম। ধূমপান ছাড়ার জন্যই মূলত ভেপিং শুরু করি। এখন ধূমপান অনেকটাই কমে গেছে। ভেপিং আমাকে ধূমপান ছাড়তে সহায়তা করছে।'
নতুন বাজারে ভেপ কিনতে আসা তানভীর আহমেদ বলেন, 'আমি ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পারছিলাম না । বন্ধুর পরামর্শে আমি প্রথম বার ভেপ ব্যবহার শুরু করি শুরুতে একটু অদ্ভুত লাগলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, এটা ধূমপানের চেয়ে অনেক ভালো বিকল্প গন্ধ নেই, ছাই নেই, আর বিভিন্ন ফ্লেভার থাকায় স্বাদেও বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড়কথা, আমি এখন ধূমপান ছাড়তে পেরেছি।' তবে ভেপ পণ্যগুলো কতটা মানসম্পন্ন বা ক্ষতিকর কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তার।
বিশ্লেষক মত: জানতে চাইলে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, শুধু আমদানি নিষিদ্ধ করেই ভেপের বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিবেচনায় কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। তিনি বলেন, বর্তমানে অবৈধভাবে ভেপ আমদানি ও বিক্রির ফলে সরকার বিপুল রাজস্ব হারাচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নিম্নমানের পণ্য বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে উপযুক্ত শুল্ক কাঠামো ও নীতিমালা থাকলে এটি রাজস্বের বড় উৎস হতে পারে এবং সঠিক মান নিয়ন্ত্রণও সম্ভব ।
বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বেন্দ্রষ্টা) সভাপতি সুমন জামান বলেন, ২০১৯ সালে ভারতে নিষিদ্ধ করার পরও ভেপের কালোবাজার বিস্তৃত হয়েছে। এর ব্যবহার কমেনি, বরং নকল পণ্যের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়েছে এবং সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে । বাংলাদেশেও প্রায় একই চিত্র দেখা যাচ্ছে।তিনি বলেন, গ্লোবাল স্টেট অব টোব্যাকো হার্ম রিডাকশনের (জিএসটিএইচআর) এক গবেষণায় দেখা যায়, নিউজিল্যান্ডে ভেপ ব্যবহার বাড়ায় ধূমপান ব্যাপকহারে কমে এসেছে। দেশটিতে ১৯৭৬ সালে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে ধূমপায়ীর হার ছিল ৪০ শতাংশ। ২০২৩ সালে এ হার কমে ৮ দশমিক ৩ শতাংশে নেমেছে।
অন্যদিকে, একই বছরে ভেপ ব্যবহারকারীর হার বেড়ে ১১ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে । যেটি ২০১৬ সালে ছিল ১ দশমিক ৪ শতাংশ। সঠিক নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে ধূমপান কমানোর এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশেও ভেপ নিয়ে বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসংগত নীতিমালার মাধ্যমে ধূমপান অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।