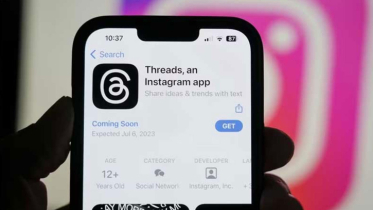সংগৃহীত ছবি
বাংলায় নারী জাগরণ এবং ক্ষমতায়নে যাঁরা কাজ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ড. নীলিমা ইব্রাহিম। তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং সমাজকর্মী। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনে তাঁর অবদান এবং ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি' বইয়ের মাধ্যমে এ সকল নারীদের সংগ্রাম যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি- সবকিছুতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন মহীয়সী এই নারী।
১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর বাগেরহাটের মূলঘর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্ম নীলিমা ইব্রাহিমের। তাঁর আসল নাম নীলিমা রায় চৌধুরী। বাবার নাম প্রফুল্ল রায় চৌধুরী এবং মা কুসুম কুমারী দেবী। নীলিমার বাবা পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন। তবে সেই সাথে থিয়েটারের প্রতি তার অগাধ আগ্রহ ছিল। জীবনে বেশ লম্বা সময়ের জন্য খুলনা নাট্য মন্দিরের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। থিয়েটারের প্রতি এই ভালোবাসা নীলিমা ও তার বাকি সন্তানদের মনেও সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করেননি বাবা।
নীলিমা ইব্রাহিম ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। খুলনা করোনেশন গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন চারটি বিষয়ে লেটার নিয়ে। পরবর্তীতে তিনি কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট থেকে আইএ এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বিএবিটি শেষ করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাস করেন।
এমএ শেষ করে লরেটো হাউজ এবং ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৪৫ সালে নীলিমা প্রথম নারী হিসেবে বিহারীলাল মিত্র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।
১৯৪৫ সালে তাঁর বিয়ে হয় তৎকালীন ইন্ডিয়ান আর্মি মেডিকেল কর্পসের ক্যাপ্টেন ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সাথে। বিয়ের পরে তাঁর নাম নীলিমা রায় চৌধুরী থেকে হয়ে যায় নীলিমা ইব্রাহিম। আর এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত। নীলিমার শ্বশুরবাড়ি ছিল ঢাকার গেণ্ডারিয়ায়, যেখানে তাঁর প্রথম সন্তান জন্ম নেয়। তবে স্বামীর বদলি চাকরির কারণে বিভিন্ন সময়ে পিরোজপুর, যশোর, বরিশাল এবং খুলনাতেও গিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে নীলিমা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট শেষ করেন তখন তিনি পাঁচ কন্যার জননী- খুকু, ডলি, পলি, বাবলি ও ইতি।
বাবার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হওয়ার দরুণ ছোটবেলা থেকেই নীলিমার ভালোবাসা জন্মে এই বিষয়ে। আর কালের আবর্তনে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করার সুযোগ হয়, তখন গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে ‘সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক' স্থির করেন। নীলিমা তাঁর গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দুটি বইও লিখেছেন। এগুলে হলো- ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত ‘ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক’ এবং ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ‘বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা'।
দ্বিতীয় বইটি লেখা হয় বাংলা সাহিত্যের ৮১ জন নাট্যকারের কাজের উপর ভিত্তি করে। লেখার ভালো মান এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের একমাত্র সংকলন হওয়ার কারণে আজও বইটি সাহিত্যের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট প্রয়োজনীয় এবং নির্ভরযোগ্য একটি তথসূত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এই দুটি ছাড়া তাঁর লেখা আরো কিছু গবেষণাগ্রন্থ হলো- শরৎ প্রতিভা (১৯৬০), বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১), বেগম রোকেয়া (১৯৭৪), বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৮৭) এবং সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ (১৯৯১)।
নীলিমা ইব্রাহিমের লেখা নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি হলো- দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪), যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪), রোদ জ্বলা বিকাল (১৯৭৩) এবং সূর্যাস্তের পর (১৯৭৪)। ‘দুয়ে দুয়ে চার’ এবং ‘রোদ জ্বলা বিকাল’-এর মূল আলোচ্য বিষয় সামাজিক বৈষম্য। ‘যে অরণ্যে আলো নেই’ ছিল একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক যেখানে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসলে মুক্তিযুদ্ধের সময় যৌন নির্যাতনের শিকার সেই নারী নিজের পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।
নীলিমার লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), এক পথ দুই বাঁক (১৯৫৮), কেয়াবন সঞ্চারিনী (১৯৬২) এবং বহ্নিবলয় (১৯৮৫)। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন এবং কিছু বিদেশি বই অনুবাদও করেছেন।
নীলিমা ইব্রাহিমের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কালজয়ী গ্রন্থ হলো ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ নামক বইটি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই দেশের নারীদের উপর যে অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতন করা হয় সেসবের একটি প্রামাণ্য দলিল নীলিমার এই বই। পাকিস্তানিদের বর্বরতার শিকার হয়ে, আবার বিভিন্ন সময়ে নিজ দেশের রক্ষণশীল সমাজের মানুষদের কাছে নিগৃহীত হতে হয় অনেক বীরাঙ্গনাকে। নীলিমা ইব্রাহিম সমাজের পরোয়া না করে বিভিন্ন সময় মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার এসকল নারীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের নারকীয়, বর্বর অভিজ্ঞতা টুকে রাখতেন দিনপঞ্জীতে। জনসমাজে এসকল বীরাঙ্গনার মন-মানসিকতা, নিপীড়ন এবং নির্যাতনের বাস্তব কাহিনী তুলে ধরার প্রচেষ্টায় প্রকাশ করেন এই গ্রন্থ।
বইয়ে নির্যাতিত বাঙালি নারীদের সংগ্রাম, দুঃখ ও শোকের কাহিনির পাশাপাশি নীলিমা ইব্রাহিমের নারীর মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতাও ফুটে উঠেছে। ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ মূলত ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এই দুটি খণ্ড নিয়ে একটি অখণ্ড বই প্রকাশ করা হয়। বলা বাহুল্য, এখানে লেখক নীলিমা বীরাঙ্গনাদের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা রক্ষার্থে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করেছেন।
১৯৫৬ সালে যখন তিনি প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন, তখন বাংলাদেশে তথা পূর্ব বাংলায় সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে পাকিস্তানি বাহিনীর শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে। এ সময়ে তিনি পাঠদানের পাশাপাশি নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালনে পাকিস্তানি বাহিনী বাধা দিলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে এর বিরোধিতা করেন। আর ১৯৬৪ সালে দাঙ্গা হলে সাধারণ জনগণের সহায়তায়ও এগিয়ে যান। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সেই সময়ের অনেক ছাত্রনেতাকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজ দায়িত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাবার এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।
স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নতুন গঠিত বাংলাদেশ সরকারের জন্য এটাও ছিল একটি জটিল সমস্যা। এই বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন কে এম সোবহান। নীলিমাও এই বোর্ডের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। এই পুনর্বাসন বোর্ডে যুক্ত হওয়ার সুবাদে এবং ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি বন্দীদের সাথে দেশত্যাগ করা ধর্ষণের শিকার কিছু নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাওয়ায় নীলিমা তাদের উপর চালানো মর্মান্তিক নির্যাতনের কথা জানতে পারেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
সেই সময় বাংলা একাডেমিতে বিশৃঙ্খলার কমতি ছিল না। এর মধ্যে আবার মকবুল নামে এক ভণ্ড এসে একাডেমির চত্বর দখল করে বসে থাকে। এই মকবুলের সাথে ছিল একটি বিশাল ও সুসংগঠিত দল। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ১৪২টি চাঁদা আয়ের বাক্স বসানো হয় এই মকুবলের নির্দেশে যেখানে জমা হওয়া চাঁদা সকলে ভাগাভাগি করে নিত। বাক্সগুলো সর্বদা দলের সদস্যদের তত্ত্বাবধানেই থাকত। প্রশাসনের সহায়তায় নীলিমা এই পুরো দলকে নির্মূল করেন, আর সেই সাথে বাকি অনিয়ম ও অরাজকতাও।
এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম। তিনি একাধারে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন (১৯৭১-৭৫) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রভোস্ট (১৯৭১-৭৭)। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভাপতি হন ড. নীলিমা। তাঁর উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় মহিলা সমিতির মিলনায়তন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়মিত নাটক উপস্থাপন করা শুরু হয় সেখানে যা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন এবং সমাজকল্যাণমূলক ও নারীর উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত ছিলেন তিনি।
সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও অনিয়মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে গিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে নীলিমাকে কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয়। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকারবিরোধী ‘মাগো আমি কোয্যাবো’ শীর্ষক উপসম্পাদকীয় লেখার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়। হাইকোর্টে গিয়ে জামিনের আবেদন করলে তাঁকে পোহাতে হয় নানা ঝামেলা। অবশেষে নিম্ন আদালত আইনজীবীদের তোপের মুখে পড়ে নীলিমাকে জামিন দিতে বাধ্য হয়।
সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও অনিয়মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে গিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে নীলিমাকে কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয়;
সমাজসেবা এবং সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কারণে বিভিন্ন সম্মাননাও পেয়েছেন নীলিমা। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জয় বাংলা পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৭), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৯), বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি পদক (১৯৯০), অননয় সাহিত্য পদক (১৯৯৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার (১৯৯৭), শেরে বাংলা পুরস্কার (১৯৯৭), থিয়েটার সম্মাননা পদক (১৯৯৮) এবং একুশে পদক (২০০০)।
২০০২ সালের ১৮ জুন না ফেরার দেশে চলে যান ড. নীলিমা ইব্রাহিম। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৮১ বছর।